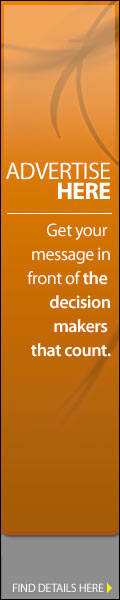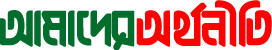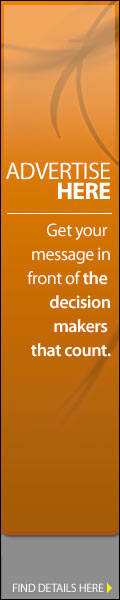
সামন্তবাদী ঢাকা শহর আবুল হোসেনের জন্য নিতান্তই অপ্রশস্ত ছিল
বোধ হয় আড়াই হাজার, যাদের মধ্যে পাঁচশ’ জন ছাত্রী, এবং শিক্ষকের সংখ্যা একশ’র বেশি নয়। পারস্পরিক পরিচয় ছিল সহজ। আবাসিক হলে সাংস্কৃতিক জীবন ছিল বেশ সরব। তবে মেয়েরা যে খুব নিশ্চিত ছিল না সে তো বোঝা যায় মেহেরুন্নেসার জন্য অনভিপ্রেত ওই ঘটনা থেকেই।
কিন্তু সহপাঠীদের কথা তো উঠেছে আসলে আবিদ হোসেন প্রসঙ্গেই। সেখানেই ফেরৎ যাওয়া যাক। ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সেদিন ক্লাসে তার পাঠদানের আগে চেয়ারে বসে পাশে তার বইভর্তি ব্যাগটি রেখে আবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আর ইউ দি সান অব সৈয়দ আবুল হোসেন?’ আবিদ তো সকল অবস্থাতেই সপ্রতিভ, সে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘ইয়েস স্যার। বাট আই ডু নট কল মাইসেলফ সৈয়দ বিকজ মাই ফাদার ডিড নট ইউজ দ্যাট টাইটেল’। আমাদের স্যার যে তার নিজের সৈয়দত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এটা তখন প্রায় সবাই জানত, যে জন্য আবিদের ওই জবাবটা স্যারের জন্য নিশ্চয়ই কিছুটা বিব্রতকর হয়েছিল। সেটা টেরও পাওয়া গেল, যখন তিনি ব্যাগ খুলে বই বের করে দ্রুত পাঠদানে মনোযোগ দিলেন। কথা বাড়ালেন না। অথচ আবিদের গলার স্বরে যেকোনো ঔদ্ধত্য ছিল তা নয়, তাকে বেয়াদবও বলবার উপায় ছিল না, সে একটি তথ্য জানাচ্ছিল মাত্র, তার পিতা সৈয়দ হয়েও নিজেকে সৈয়দ বলতেন না, তাই পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণে সেও নামের ওই অগ্রভাগকে ধারণ করে না, এটি একটি বাস্তবিক সত্য বটে; কিন্তু আমরা যারা আমাদের শিক্ষককে জানতাম তাদের মনে হয়েছিল জবাবটা তার পছন্দ হয়নি। তবে আবিদ তো নাচার, তার পক্ষে তো আর সৈয়দ আবিদ হোসেন হওয়া সম্ভবপর নয়।
আবিদকে সেদিন বিশেষভাবেই জানলাম। দেখলাম তার সপ্রতিভতা, নামান্তরে বলা চলে সৎ সাহস। আর এটাও জানা হয়ে গেল যে তার পিতা ছিলেন ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আবুল হোসেন, যার সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়েই অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। লেখক হিসেবে যিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীমান ও সাহসী। কিন্তু ঢাকাতে তিনি থাকতে পারেননি, তার ওই সাহিত্যচর্চার কারণেই। ঢাকার নবাববাড়ির লোকেরা অবাঙালিই ছিল, নিজেদেরকে তারা সেভাবেই দেখত, বাংলা পড়তে জানত না, শিখবার চেষ্টাও করেনি; আবুল হোসেনের কোনো লেখাই তাদের পড়বার কথা নয়, নিশ্চয়ই পড়েওনি, কিন্তু তাতে কি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও ঢাকার তো তারাই মালিক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাদের নাম জড়িত থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা বলতে কিছুই ছিল না, বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী চিন্তা হচ্ছে এমন আভাস পেলে তারা ক্ষিপ্তই হতো। অধ্যাপক আবুল হোসেনকে তারা ডেকে পাঠিয়েছিল, এবং তিনি যে ধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন তা আর লিখবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিতে বলেছিল। আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং লেখক, তার পক্ষে লাঠিয়ালদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরা সম্ভব ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য তাই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বের হয়ে এসেছেন, এবং তারপরে বিলম্ব না করে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে গেছেন। আইনশাস্ত্রে তার উচ্চডিগ্রি ছিল, কলকাতায় গিয়ে তিনি সসম্মানে ওকালতি পেশায় যোগ দিয়েছেন, এবং লেখা থামাননি। তবে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেননি, মাত্র ৪২ বছর বয়সে (১৮৯৬-১৯৩৮) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।
সামন্তবাদী ঢাকা শহর আবুল হোসেনের জন্য নিতান্তই অপ্রশস্ত ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে কিছুটা মুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন সেটা ঠিক, কিন্তু নবাববাড়ির লাঠিয়ালদের আক্রমণে সে পরিবেশকে যখন বিপন্ন হতে দেখলেন তখন তার ভেতর নিশ্চয়ই প্রচ- ঘৃণা ও অভিমানের উদ্রেক হয়েছিল, যে জন্য এখানে তিনি আর থাকবেন না বলেই ঠিক করেছিলেন। তার পুত্র আবিদ হোসেনও থাকেনি, সেও এখানকার পড়াশোনা শেষ করে দ্রুত চলে গেছে আরও বড় জায়গায়, লন্ডনে এবং পিতার মতোই ঠিক করেছে ওকালতি করবে। তবে তার জন্য ক্ষেত্রটা ততদিনে প্রশস্ত হয়ে গেছে, কলকাতার বদলে সে পেয়েছে লন্ডন, পিতার এমএবিএল-এর বদলে বার-এট-ল। ১৯৫৯-এ আমি যখন প্রথমবার ইংল্যান্ড যাই তখন আবিদ সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে ব্যস্ত, খ-কালীন চাকরি করে বইয়ের দোকানে, অনুষ্ঠান করে বিবিসি’র বাংলা বিভাগে। ১৯৬৫তে দ্বিতীয় বার গিয়ে আবিদকে দেখি নিজেকে বেশ গুছিয়ে এনেছে, এবং ঠিক করেছে ব্যারিস্টারিটা হয়ে গেলেই দেশে ফিরবে। সেই প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করেছিল, নিজের কাছে, এবং দেশের কাছে। ফিরে এসেছিল, উনসত্তরের শেষে। পূর্ববঙ্গ তখন কাঁপছে। তার দেশপ্রেম ছিল প্রবল। ভেবেছিল থাকবে। কিন্তু থাকতে পারেনি। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হবার পরে ফেরত চলে গিয়েছিল লন্ডনে। দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই যে ওখানে তার জন্য করার মতো অনেক কাজ রয়েছে। কিন্তু পারেনি। পিতার চেয়েও অল্প বয়সে সে মারা গেছে।
লন্ডনে নতুন বাসা ঠিক করেছিল; সেখানে সিঁড়ি বেয়ে আসবাবপত্র তোলার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমাদের অকৃতদার এই বন্ধুটি কোনো পারিবারিক উত্তরসূরি রেখে যায়নি, তবে সে আছে এবং থাকবে, আমাদের অনেকেরই স্মৃতিতে।
লেখক : অধ্যাপক ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদনা : জব্বার হোসেন