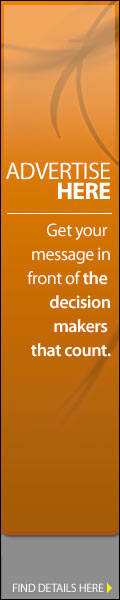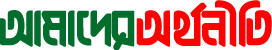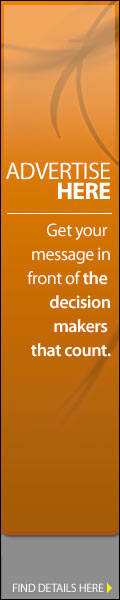
দুর্গাপূজার দার্শনিক তাৎপর্য
বিপ্লব হালদার
মাতৃভাবে পরম সত্যের আরাধনা অত্যন্ত প্রাচীন। ঋগে¦দীয় ‘দেবীসূক্তে’ তিনি সমগ্র বিশ্বের সম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে দেবী-মাতৃকাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আরাধনা করা হয়। দুর্গারূপে তার আরাধনা বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। শরৎকালে মৃনম্গঈ প্রতিমায় খুব ধূমধামের সঙ্গে তার পূজা করা হয়। মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেব-দেবীর আরাধনা বাংলার বৈশিষ্ট্য। ‘নবরাত্রি’ বা ‘দশেরা’র সময় প্রতিমাতে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। শুক্লাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেলগাছের তলায় তার বোধন করা হয়। পরদিন সকাল এবং আরও পরবর্তী দুদিন ধরে বিভিন্ন স্থান থেকে আহরণ করা জল দিয়ে দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হয় এবং বিশদভাবে নানা উপচারে বিধিবদ্ধ প্রথায় তাকে আরাধনা করা হয়। দশমী তিথিতে দেবী প্রতিমাকে নদী অথবা পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। তারপর শান্তি ও আশীর্বাদ প্রার্থী সকলের মধ্যে শান্তিজল ছেটানো হয়, যার দ্বারা এই আড়ম্বরপূর্ণ মহোৎসবের সমাপন সূচিত হয়। কারো কারো মতে, এই উৎসব অতীতে রাজন্যবর্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত ‘রাজসূয়’ যজ্ঞের নিদর্শন। অন্যান্য দেব-দেবী পরিবৃত দেবী দুর্গার এইরূপে প্রতিমা পূজার প্রথাটি অন্তত হাজার বছরের প্রাচীন, যদিও সাধারণভাবে এটি পরবর্তীকালের মনে করা হয়।
প্রতিমায় পূজা কেন?
বেদান্ত অনুসারে, পরম সত্য নির্গুণ এবং নাম ও রূপের অতীত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে, সেই পরম সত্যই আবার নানা দেব-দেবীর রূপ ধারণ করেন। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, সেই পরম সত্য বহুবিধ দেব-দেবীর রূপে প্রকাশিত হন। যদিও প্রতিটি দেব-দেবী ঈশ্বরের এক একটি ভাবের অধিষ্ঠাতা বা অধিষ্ঠাত্রী, সাধারণভাবে সৃষ্টির বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ও এদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। মুনি-ঋষিরা যোগযুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের যে যে রূপ দর্শন করেছিলেন সেগুলির সাকার বিগ্রহ এই মূর্তি। শিল্পকলা এগুলিকে সুন্দর ও ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। পরবর্তী কালে অনেক শিল্পী অনেক দেব-দেবীর চিত্র রচনা করেছেন এবং সেগুলো আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ। ভক্তি-ভাবনার মূর্ত প্রকাশের কেন্দ্র বিন্দু হওয়ায় মূর্তিগুলি বিভিন্ন মানসিকতার ভক্তদের তৃপ্ত করে। কিন্তু মূর্তিগুলি শিল্পীমনের স্বাভাবিক প্রকাশমাত্র নয়, সেগুলি পরম দৈবী সত্তার প্রতীক। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে দৈবীভাবে প্রবুদ্ধ করা, আমাদের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্তি দেওয়া নয়। যেহেতু মূতিরগুলি সাধক শিল্পী দ্বারা সৃষ্ট, তাই সেই মূর্তিগুলির রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও কোনো না কোনো গভীর চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করে। এই সত্য যখন শিল্প সুষমায় আমাদের কাছে পরিবেশিত হয় তখন তা অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। ‘মূর্তিগুলি’ দর্শনের বিমূর্ত ধারণা এবং অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মূর্তরূপ। এগুলিই অসীম এবং সসীমের মধ্যে, নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে, সাকার এবং নিরাকারের মধ্যে সংযোগকারী। আমরা যদি মূর্তিগুলির যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি তবে আমরা খুব সহজেই এর অন্তর্গুঢ় সত্যতে পৌঁছাতে পারি, কারণ ধ্যান তখন অনেক বেশি সহজসাধ্য হয়। একজন ভক্তের কাছে ঈশ্বরের মনুষ্যরূপ বিগ্রহ এতই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে তিনি তার মধ্যে ঈশ্বরকে খুব কাছের এবং প্রিয়জন হিসেবে মনে করেন। অধ্যাত্ম সাহিত্যে এরকম শত শত উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে ভক্ত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জননী, সন্তান ইত্যাদি নানারূপে দর্শন করেছেন।গোপীদের দুর্গাপূজা
শ্রী পতিত উদ্ধারণ গৌর দাস ব্রহ্মচারী
শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার আশায় গোপীদের কাত্যায়নী ব্রতের উল্লেখ রয়েছে। শুকদেব গোস্বামী বললেন, হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোকুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাত্যায়নীর অর্চনাব্রত পালন করলেন। সারা মাস তারা কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করেছিলেন। হে রাজন, সূর্যোদয়কালে যমুনার জলে স্মান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তারপর তারা ঘঁষা চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুপারী, নব পল্লব, সুগন্ধ মাল্য ও ধূপসহ নানা প্রকার উপহারের দ্বারা তার পূজা করেছিলেন।
‘হে দেবী কাত্যায়নী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তিধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিয়ন্তা, অনুগ্রহ করে নন্দমহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।’ এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণ প্রত্যেকে তার পূজা করছিলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, এই শ্লোকে উল্লিখিত দেবী দুর্গা বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া নন, বরং যোগমায়ারূপে পরিচিত ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। অনেকে মনে করেন ‘মহামায়া’ ও ‘দুর্গা’ শব্দে বহিরঙ্গা শক্তিকেই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তা সত্য নয়। বৃন্দাবনে গোপীগণ সেই অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকেই আরাধনা করেছিলেন। আর যদি কেউ বলে যে, গোপীগণ বহিরঙ্গা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। তাতেই বা ক্ষতি কীসে? গোপীদের কী উদ্দেশ্য ছিল তা আমাদের বুঝতে হবে। সাধারণত মানুষ দুর্গাপূজা করে কোনো জাগতিক লাভের আশায়। কিন্তু গোপীগণ এখানে কৃষ্ণকে লাভ করার আশায় দুর্গাপূজা করেছিলেন। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা যে কোনো উপায় অবলম্বনে প্রস্তুত ছিলেন। সেটিই ছিল গোপীদের অত্যুৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভের আশায় তারা পুরো একমাস যাবৎ দুর্গাপূজা করেছিলেন।
আমরা যদি মূর্খের মতো তাদের কার্যাবলিকে কোনোভাবে জাগতিক মনে করি, তবে কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।