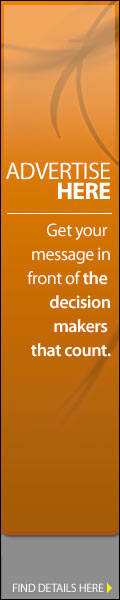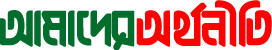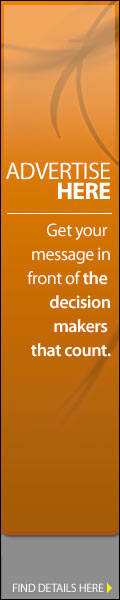
বৌদ্ধধর্মে ব্যক্তি স্বা ধীনতা ও মানবাধিকার
তহনংকর ভিক্ষু
মানবধিকার প্রসঙ্গে বুদ্ধবচনের সারমর্ম কবিগুুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সুন্দররুপে পেয়ে থাকি। ‘বুদ্ধদেব’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেনÑ“বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল;পরস্পর হিংসা ও জাতিভেদের সাংঘাতিক ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই তাঁরই বাণীতে আজ আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষে কলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজাঁর বেদীতে আর্বিভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে আবারো উন্মোচন করার জন্য। বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকার ভেদ ছিল? কেউ ম্লেচ্ছ? কেউ কী ছিল অনার্য? তিনি তার সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষের জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।”
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবধিকার ও ধর্ম পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। মানুষের কল্যাণের স্বার্থে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মানবমুক্তির সার্বজনীন বাণী নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মগুরু তথা মণীষীদের আর্বিভাব। ধর্মো উৎপত্তির পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায়, যখনই বিভিন্ন অব্যবস্থা, অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে মানব সমাজ চরম কলঙ্কিত হয়ে উঠে, তখনই সমষ্টিগত কল্যাণের সার্বজনীন মঙ্গলের বাণী নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকগণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
ধর্ম ও মানবতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষের সহজাত মানবিক অনুভূতি ও ধর্মীয় চেতনার সমন্বিত রুপ হলো মানবতাবাদ। আর মানবতা হলো মানবাধিকার রক্ষার মহান উপায়। বাস্তবে ধর্মীয় বিশ্বাস, কতকগুলো নৈতিক ও দার্শনিক মূল্যবোধ আরোপের মাধ্যমে মানুষের মানবিক অনুভূতিগুলোকে জাগ্রত করেই মানবতাবাদের জন্ম দেয়। সাধারণভাবে ধর্ম বলতে বোঝানো হয়, কোন অদৃশ্য শক্তির প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আনুগত্যশীল নানা ক্রিয়াকলাপ, যেমনÑউপসনা, পূজা ইত্যাদি। ধর্ম সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী লর্ড যাগলান বলেছেন,“অতি প্রকৃতকে কেন্দ্র করে যেসব বিশ্বাস এবং ক্রিয়াকারে উদ্ভব হয়েছে, সে সব কিছুর সমষ্টিই হলো মানুষের ধর্ম। কিন্তু পৌত্তলিকতা বা অদৃশ্য শক্তির আরাধনাময় পূজা অনুষ্ঠান গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ নয়। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছেÑ“স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহি পস্সিকো, ওপনয়িকো. পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞুহীতি।’ অর্থ্যাৎ, বুদ্ধের ধর্ম (১) সুব্যাখ্যাত, (২) সান্দিষ্টিক বা প্রত্যক্ষ করণীয়, (৩) অকালিক বা কালাকালহীন ফলদায়ী, (৪) ‘এসো ও দেখো’Ñবলে আহবানযোগ্য, (৫) উপনায়ক সদৃশ (অর্থ্যাৎ বুদ্ধের অবর্তমানে উপনায়ক সৃশ) বা ঔপন্যায়িক (অর্থ্যাৎ তির্যক, প্রেত, অসুর ও নরক দ্বার রুদ্ধ করণে ও আর্যমার্গ আনয়নে সমর্থ) এবং (৬) বিজ্ঞব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ জ্ঞাতব্য। এই ছয়টি গুণে বিভূষিত বুদ্ধের প্রবর্তিত মানবতাবাদী ধর্ম, যেখানে অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। বুদ্ধের শিক্ষায় অনুশীলিত মানুষ শীলবান, ধার্মিক ও চরিত্রবান হন। তিনি কোনো প্রকার প্রলোভন বা বাধা বিপত্তিতে বিচলিত না হয়ে, ন্যায় ও সত্যে স্থিত থেকে মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত ও সুশোভিত হন এবং মানবাধিকার রক্ষার মধ্য দিয়ে মানবতার জয়গান করতে পারেন।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আড়াই হাজার বছর আগের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য বা জাতীভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। যা ছিল মানবতা ও মানবাধিকারের সম্পূর্ন বিপরীত। আড়াই হাজার বছর পূর্বে সমাজে প্রচলিত এই জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা ছিল চতুবর্ণÑব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ভিত্তিক। তৎকালীন হিন্দু সমাজের এই চারি বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও বিভিন্ন অধিকারের ক্ষেত্রে মারাত্মক বৈষম্য পরিলক্ষিত হতো। সমাজে মান-সম্মান, নানা সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যতা প্রচলিত হয়েছিল।
“পূজিত্র বিুপ্র সকল গুলহীনা-শূদ্রন গুণাগুণ জ্ঞান প্রবীনা।
ঢোল গমার শূদ্র পশুনারী-সকল তাড়নাকে অধিকারী।”
অর্থ্যাৎ সর্ববিধ গুণহীন হলেও ব্রাহ্মণকে পূজা করবে, গুণরাজি ও জ্ঞানে প্রবীণ হলেও শূদ্রদেরকে পূজা করতে নেই। ঢোল, গ্রাম্যলোক, শূদ্র, পশু এবং নারী এরা সর্ববিধ উৎপীড়নের অধিকারী বা যোগ্য। এখানে শূদ্র ও নারীকে পশুর সমান কল্পনা করা হয়েছে।
গৌতম বুদ্ধ মানব সমাজের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উচ্চবর্ণ থেকে নি¤œবর্ণ প্রচলিত এই ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবাইকে সমান গুুরুত্ব দিয়ে সকল মানুষকেই মুক্তির আহবান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধ বজ্রনিনাদে ঘোষণা করেছিলেÑা জন্মের জন্য অথবা মাতা বিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য আমি কাউকে ব্রাহ্মণ বলি না; সে ভোবাদি হতে পারে, সে ধনবানও হতে পারে, কিন্তু যার কিছুই নেই, যিনি অনাসক্ত, যিনি অক্রোধী, ব্রতবান, শীলবান, তৃষ্ণাহীন, দান্ত, অন্তিম দেহধারী, তাঁকেই আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলি। বুদ্ধ ‘সুত্তপিটকে’র ‘ধম্মপদে’ ব্রাহ্মণবর্গে কাকে ব্রাহ্মণ বলা হয় বা প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম নিলেও কেউ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয় না। মেথর প্রভৃতি ঘরে জন্ম নিলেও কেউ বৈশ্য, শূদ্র, বা মেথর হয়ে যায় না। কর্মই মানুষকে পদবাচ্যের অধিকারী করে তোলে। তাই বুদ্ধ ধর্মপদের ব্রাহ্মণ বর্গে বলেছেনÑ
ন জটাহি ন গোত্তন ন জচ্চ হোতি ব্রাহ্মণো, যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূচি সো চ ব্রাহ্মণো।
অর্থ্যাৎ জটা, গোত্র ধারী বা জন্মের বংশ পরিচয় দিয়ে কেউ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে পারে না। একমাত্র স্বকীয় সৎকর্ম ও ধর্মনীতি আচরণের দ্বারা, যাঁর কায়, বাক্য ও মনে পাপ নেই, যিনি প্রগাঢ় ধ্যানী, ধীমান, সত্যাসত্য নির্ণয়ে পারদর্শী, পরমার্থ লাভ করেছেন, শত্রুদের মধ্যে যিনি মৈত্রী ভাবাপন্ন, হিংসাপরায়ণদের মধ্যে যিনি অহিংস ও সত্যাবাদী, প্রসন্ন চিত্তসম্পন্ন, নিস্পাপ, সংশয়হীন ও নির্বাণ প্রাপ্ত তিনিই প্রকৃত সাধু, তিনিই ব্রাহ্মণ। যদি ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করে নিরাসক্ত হয় এবং অবিদ্যা নাশ করে সত্যোপলিব্ধ করে, তবেই তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্যের যোগ্য। অতএব যারাই এক্ষেত্রে বৈশ্য, শূদ্র বা ক্ষত্রিয়, তাঁরাও অনুুরুপ সততা ও সৎকর্মের আচরণ দ্বারা সাধু মানুষ বা ব্রাহ্মণ পদবাচ্যের অধিকারী হতে কোন বাধা নেই।
বৌদ্ধ ধর্মে ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুুরুষ সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বর্ণবৈষম্য ও জাতিবেদ প্রথার বিুরুদ্ধে বুদ্ধ আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বাকস্বাধীনতায় ও শিক্ষা অর্জনের অধিকার বৌদ্ধধর্মে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। এমনকি গৌতম বুদ্ধ তাঁর নিজের ধর্মমতকেও গণতান্ত্রিক মতবাদে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সে সাথে রয়েছে নর-নারীর সমধিকারের প্রশ্ন। বৌদ্ধধর্মে নারীর অধিকার স্বীকৃত। ভিক্ষুসংঘে নারী স্থান পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মে জীবনের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির সাথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। বৌদ্ধ ইতিহাসে ভিক্ষুণীরা ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে এবং বৌদ্ধ নারীরা সমাজ ও দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও নারীদের সমানধিকার স্বীকৃত। জীবনের সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় গৌতম বুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যথেষ্ট পরিমান গুুরুত্ত্বারোপ করেছে।
লেখক : সাংগঠনিক সম্পাদক বুড্ডিস্ট মং সোসাইটি
উপধ্যক্ষ ও নব পন্ডিত বিহার,চট্টগ্রাম।