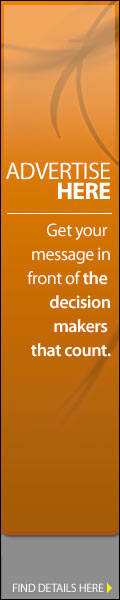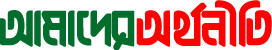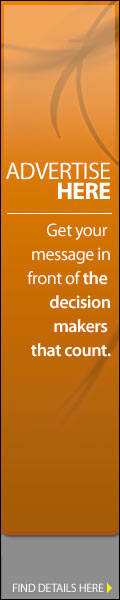
অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন যে তিনজন তাদের গবেষণার মূল এই কথাটিই অর্থনীতির কল্যানেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের কাছ থেকে আলগা হতে হবে

জয়দীপ বিশ্বাস
বাজার-নিয়ন্ত্রিত একটি দেশের অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য, স্থিতিশীলতা ও সুস্থিত বিকাশ নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য দরকার নিরপেক্ষ ও দক্ষ এক তৃতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতিতে এই নিয়মিত নজরদারির দক্ষতা কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে বেশি আছে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক না কি সরকার? প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তরদাতা ভাবতেই পারেন যে, এই প্রতিতুলনার তো আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই। প্রথমত, যে কোনও দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ফলে এখানে সরকারের সঙ্গে উদ্দেশ্যের সংঘাতের কোনও সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান, তাতেই বা কী! দুটোই তো দেশের অর্থনীতির কল্যাণেই কাজ করছে। ফলে দুই পক্ষেরই সমান্তরাল নজরদারি চলুক না!
হ্যাঁ, যুগপৎ নজরদারি চলতেই পারে। কিন্তু তাতে আমাদের মৌলিক প্রশ্নের জবাব কিন্তু মিলছে না। কারণ, বিষয়টা শুধু নজরদারির নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নও। আর হেঁয়ালি না করে এবার একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণ লোকজনও আজকাল এটুকু বোঝেন যে, ব্যাংকের সুদের হারে কৃত্রিমভাবে ওঠা-নামা তৈরি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সার্বিক মূল্যস্তর সুস্থির রাখার পদক্ষেপ করে। আবার, অর্থনীতিতে ঝিমুনির ভাব যদি ধরা পড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে ব্যাংক ঋণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য নির্দিষ্ট গুচ্ছ লক্ষ্য রয়েছে। সেগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিস্থিতি বুঝে তারা ব্যবস্থা নেয়। কোনও একটি দেশের কথা ধরা যাক যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যক ব্যাংকগুলোতে এমনিতেই অনাদায়ী ঋণের গভীর সমস্যা রয়েছে। লগ্নিযোগ্য আর্থিক সম্পদ আটকে থাকার ফলে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না। অথচ এই অবস্থায় দেখা গেল সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বলছে যে, সুদের হার কমিয়ে এক লপ্তে আরও বেশকিছু পরিমাণ টাকা বাণিজ্যক ব্যাংকগুলোতে ঢালতে হবে। তবেই নির্ঘাৎ ব্যবসায়ী ও উৎপাদক গোষ্ঠী উৎসাহিত হবে। নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে। অর্থনীতির চাকা মসৃণভাবে গড়াবে।
দেখা গেল, যৌথ নজরদারির মাধ্যমে অর্থনীতিতে রোগের লক্ষণ দুই পক্ষের কাছেই সঠিকভাবে ধরা পড়ছে। কিন্তু দাওয়াই বাছতে গিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতান্তর তৈরি হচ্ছে।
বাংলাদেশ, ভারত এমনকি পাকিস্তানেও রিজার্ভ ব্যাংক ও সরকারের মধ্যে এমন মতবিরোধ দেখা গেছে। ভারতে তিন বছরের মেয়াদের মাঝামাঝিতেই ২০১৮-র শেষের দিকে উর্জিত প্যাটেলের ইস্তফা এবং এর মাস দুয়েক আগে কেন্দ্রের খবরদারির সমালোচনায় রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্যের বিস্ফোরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। আরও একটু পিছিয়ে গেলে আমাদের মনে পড়বে যে, উর্জিতের পূর্বসূরি রঘুরাম রাজন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান হিসেবে তাঁর অন্তিম ভাষণে সরকারকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, দেশের অর্থনীতিকে যদি একটি গাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সেই গাড়ির চালকের সিট-বেল্ট। এমনিতে না বাঁধলে ক্ষতি নেই। কিন্তু গাড়ি যদি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তখন প্রাণ বাঁচাতে এই সিট-বেল্টের জুড়ি নেই। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের পড়ুয়াদের সামনে প্রদত্ত সেই বক্তৃতায় আকারে ইঙ্গিতে রঘুরাম এটাই বুঝিয়েছিলেন যে, ভারত সিট ব্যাল্ট বাঁধতে রাজি নয়। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সংঘাতের পেছনে যে কারণটি মূলত কাজ করে তা হচ্ছে দুটি প্রতিষ্ঠানের চরিত্রগত ফারাক।
সরকার একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জনগণের ভোটে জিতে একটি রাজনৈতিক দল বা কয়েকটি দল একত্রে সরকার গঠন করে। ফলে সরকার মনে করতেই পারে যে একমাত্র জনগণের কাছেই তারা দায়বদ্ধ। অতএব যা সরকার মনে করছে জনগণের জন্য কল্যাণকর সেই মত কাজ করার পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্ব-শাসনের কথা বলে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতেই পারে না। কিন্তু সরকার যে-কথাটা প্রায়শই মনে রাখে না তা হল এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে-কাজগুলি করার জন্য নিয়োজিত সেখানে তাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। দেশের মুদ্রা নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারের কোনও ভূমিকাই থাকা উচিত নয়। কারণ ওই কাজটিই সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং আইনি অধিকার রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে।
কিন্তু তত্ত¡গত ভাবে অর্থব্যবস্থায় সংকটমোচনে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং সেই ব্যবস্থাপত্রটি লেখার যোগ্য অধিকারী কে তা নিয়ে চাপান উতোরের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আর্থিক সংকটের সময় এবং ম্যাক্রো অর্থব্যবস্থার লক্ষ্যভেদে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা ও ঋণ নীতি মধ্যে কোনটা বেশি কার্যকর এ নিয়ে আদর্শের লড়াই চলছে যুগে যুগে দেশে দেশে। বাম মতাদর্শের কাছাকাছি থাকা অর্থশাস্ত্রীরা বলবেন যে, জন মেনার্ড কেইন্সের হাত ধরে বাজেট বরাদ্দ বাড়ালেই দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের মত বিষয়গুলো নিয়ে সমস্যা থাকে না। অন্যদিকে মিল্টন ফ্রিডমেনের অনুরাগী দক্ষিণাচারী অর্থনীতিবিদেরা চাইবেন সরকারি খরচ বাড়িয়ে নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেন সুদের হার কমিয়ে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে ফেলে। এ নিয়ে কেইন্স-ফ্রিডম্যান আর কেমব্রিজ-শিকাগো দ্বৈরথ আজও চলছে।
এখানে এই অতি-পরিচিত কথাগুলো অমোঘভাবে উঠে আসছে এবারের অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন যে তিনজন তাঁদের আজীবন গবেষণার স্বীকৃতি প্রসঙ্গে। আমেরিকার ব্রæকিংস ইনস্টিটিউশনের বেন বারনানকে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডগলাস ডায়মন্ড এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিপ ডিবভিগকে যৌথভাবে ২০২২ সালে অর্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ব্যাংক এবং আর্থিক সংকটের নিয়ে তাঁদের মৌলিক গবেষণার জন্য। নোবেল কমিটি শংসাপত্রে বলেছে যে, অর্থনীতিতে, বিশেষ করে আর্থিক সংকটের সময়ে, ব্যাংকের ভূমিকা কী এ-বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে এই ত্রয়ীর গবেষণা আমাদের সাহায্য করেছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বারনানকে-ডায়মন্ড-ডিবভিগের স্বতন্ত্র কিন্তু সমজাতীয় গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের বারবার সাবধান করেছে, ব্যাংক যাতে কোনওভাবেই দেউলিয়া না হয়।
কথা হচ্ছে, ব্যাংক কেন খামোখা ফেল মারতে যাবে! আর এ-নিয়ে অযথা উতলা হওয়াই বা কেন। ১৯৮৩-তে জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমিতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আজকের নোবেলজয়ী তিনজনের দু’জন ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বরাবরই প্রবল। আসলে ব্যাংকের সৃষ্টিতত্তে¡র মধ্যেই তার মারণ-বীজ লুকিয়ে থাকে যে!
তাহলে ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি ঠিক কেমন সেটা একবার সহজ করে বোঝা যাক। গ্রাহকদের আধুনিক ব্যাংক নানা ধরনের পরিষেবা দিয়ে থাকে। আমরা সে সবে যাচ্ছি না। মূলত ব্যাংক ব্যবসাটা করে ঋণ দেওয়া নেওয়ার। আমরা সবাই ব্যাংকের কাছে আমাদের সঞ্চয় জমা দিই। তার বিনিময়ে ব্যাংক আমানতকারীকে একটি পৃর্ব-ঘোষিত কিন্তু সময়ে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য হারে সুদ দেয়। এই সুদ হচ্ছে আমানতকারীদের আয়। কেইনস বলতেন সুদ হচ্ছে নিজের ট্যাঁকের টাকা অন্যকে হস্তান্তর করার পুরস্কার! ইন্টারেস্ট ইজ রিওয়ার্ড ফর পার্টিং উইদ লিকুইডিটি। ব্যাংকের গ্রাহকরা চাইলেই ব্যাংকে রক্ষিত তাঁদের সেভিংস একাউন্ট থেকে যে কোনও সময় আমানত তুলতে পারেন। আমানতকারীদের সুদ মেটাতে গেলে তো ব্যাংকের আয় চাই। সেই আয় আসে ব্যাংক ঋণ থেকে। যাঁরা তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে চান সেই লগ্নিকারীদের মূলধনের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যাংক থেকে প্রতিশ্রæত সুদের বিনিময়ে ঋণ। এছাড়াও, আমরা সাধারণজনরা বাড়ি বানাতে, গাড়ি কিনতে, সন্তানদের পড়াশোনা করাতেও ব্যাংক থেকে ধার নেই। বাজার অর্থনীতিতে বড় মাপের খরচ কিন্ত চার্বাকের নীতি মেনেই চলে। ঋণং কৃত্বয়া ঘৃতং পিবেৎ। তবে খটকা আসে এর পরেই। সত্যিই কি যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ? আসলে অতো সুখ সবার সয় না। অন্তত ব্যাংকের বেলা তো কদাপি নয়। সমস্যাটা তৈরি হয় ভেতর থেকেই। বলা চলে ‘তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে’! সমস্যার স্বরূপটা এরকম। ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত যে আমানত তা হচ্ছে ব্যাংকের দায় (লায়াবিলিটি)। কারণ যখনই গ্রাহক এসে তাঁর আমানতের একাংশ বা পুরোটাই উঠিয়ে নিতে চাইবেন, ব্যাংককে তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো টাকা দিতে হবে। কিন্তু ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঋণ ফেরত দেবার কথা ব্যাংক বলতে পারে না। ধরা যাক, ব্যাংক থেকে কুড়ি বছরে পরিশোধযোগ্য কুড়ি লাখ টাকার গৃহঋণ নিয়েছি। ব্যাংকের সঙ্গে আমার চুক্তি হচ্ছে প্রতি মাসে বাইশ হাজার টাকা করে ইএমআই দেব। ঋণের পূর্ণ মেয়াদ শেষে, অর্থাৎ কুড়ি বছরে গিয়ে আমি ঋণমুক্ত হব। এর মধ্যে ব্যাংক কোনও অবস্থায়ই আমার কাছে আগাম ঋণ মেটানোর জন্য চাপ দিতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকের যা সম্পদ (দীর্ঘ মেয়াদে প্রদত্ত ঋণ) তা সহজে এবং সহসা নগদে পাল্টে দেওয়া যায় না। অথচ ব্যাংকের দায় (লায়াবিলিটি) পুরোটাই লিকুইড। মানে নগদে পরিবর্তনযোগ্য। ব্যবসার ধরনটাই এমন হওয়ার ফলে ব্যাংকের সামনে বরাবর দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। কোনও এক সকালে যদি ব্যাংকের কাউন্টারের সামনে আমানতকারী সবাই এসে তাঁদের গচ্ছিত ধনরাশি ফেরত চান, পৃথিবীর সেরা ব্যাংকেও লালবাতি জ্বলবে। কারণ গ্রাহকদের জমা রাখা আমানত থেকেই তো ব্যাংক ঋণ দিয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদের সে-সব ঋণতো চাওয়া মাত্রই ফেরত পাওয়া যাবে না। স্বল্প মেয়াদের আমানত আর দীর্ঘ মেয়াদের ঋণের পরস্পর-বিরোধী আন্তসম্পর্কই ব্যাংকের গণেশ ওল্টানোর কারণ।
ডায়মন্ড-ডিবভিগ সেই পেপারে এবং ডায়মন্ড এককভাবে ২০০৭ সালে ইকনমিক কোয়ার্টারলিতে প্রকাশিত ‘ব্যাংকস অ্যান্ড লিকুইডিটি ক্রিয়েশন: অ্যা সিম্পল এক্সপোজিশন অব দ্য ডায়মন্ড-ডিবভিগ মডেল’ শিরোনামের প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন যে সরকারের আমানত বিমা প্রকল্প ব্যাংককে দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে।
আসলে ব্যাংকের সবচাইতে বড় মূলধন হচ্ছে আমানতকারীদের বিশ্বাস। গ্রাহকরা যদি জানেন যে অমুক ব্যাংক কখনও ফেল মারতে পারে না, তাহলে সেই ব্যাংক সত্যিই কখনও দেউলিয়া হবে না। তাহলে এবার প্রশ্ন দাঁড়ায় সেই বিশ্বাস আসবে কী করে? এর সহজ রাস্তা হচ্ছে আমানত বিমার ভরসা। অন্যটি অবশ্যই সরকার নিজেই যদি সেই ভরসা দেয়। ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাংক জাতীয়করণের পেছনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সেই ভরসার জায়গা তৈরি করা যাতে ব্যাংকের দরজায় তালা না পড়ে।
ব্যাংক দেউলিয়া হলে অর্থনীতিতে কতটা কু-প্রভাব পড়ে এ নিয়ে বারনানকেরা বিস্তর লেখালেখি করেছেন। বস্তুতপক্ষে, বারনানকে নিজে বেশি আগ্রহী ছিলেন অর্থনৈতিক সংকটের সময় অনা-আর্থিক প্রভাব কেমন হয় সেই গবেষণায়। ডায়মন্ড-ডিবভিগ মডেল যে বছর বেরোল সেবারই, অর্থাৎ ১৯৮৩-তে আমেরিকান ইকোনমিক রিভিউ জার্নালে বারনানকে ‘নন-মনেটারি এফেক্টস অব দ্য ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস ইন দ্য প্রোপাগেশন অব দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন’ শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এর ঠিক কুড়ি বছর আগে লেখা মিল্টন ফ্রিডম্যান ও আন্না সোয়ার্টজের বিখ্যাত বই ‘অ্যা মনিটরি হিস্ট্রি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ১৮৬৭-১৯৬০’ -এর পরিপূরক গবেষণা হিসেবে বারনানকের লেখায় আর্থিক সংকটে ব্যাংকের ভূমিকার কথা সবিস্তার ও গভীরতরভাবে উঠে আসে।
ইহুদি সন্তান বারনানকেকে কৈশোরে পারিবারিক ওষুধের দোকানে বসতে হয়েছে। পরবর্তীতে সামলেছেন আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নরসে থাকাকালীন তাঁর সাত দফা ‘বারনানকে ডকট্রিন’ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের করণীয় কাজ এবং এর স্ব-শাসনের ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেশ জুড়ে তৈরি করে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি তার বোধ ও বুদ্ধিমতো মুদ্রা নীতি প্রণয়ন করতে পারে, তাতে বাণিজ্যক ব্যাংকগুলিও তাদের সম্পদ ও দায়ের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্যের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এমন আদর্শ পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকট বা মন্দার মতো ভয়াবহতা অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যায়।
এই কথাগুলো তাঁর মতো কওে অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজন বলেছেন অনেকবার। তিনি নোবেল পান নি বটে। কিন্তু ডগলাস ডায়মন্ডের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু সমগোত্রীয় গবেষণা রয়েছে যে! এবারের নোবেল তাই প্রতীকী অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নৈতিক জয়েরই বার্তা দিচ্ছে।