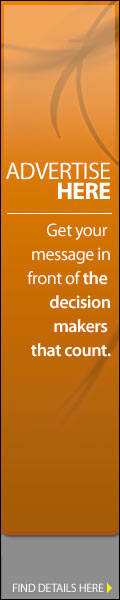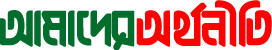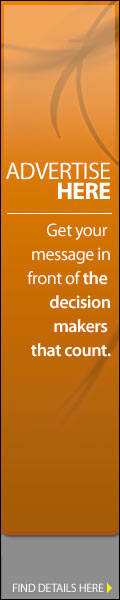
আইএমএফ’র ঋণ ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের বাস্তবতা

এবি সিদ্দিক
নাইজেরিয়ান অর্থনীতিবিদ স্যাম আলুকো তাই আইএমএফ-এর এ স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট কর্মসূচিকে মৃত্যুর চুম্বন বা ‘কিস অব ডেথ’ নামে অভিহিত করেছেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ তার ২০০২ সালে প্রকাশিত বই ‘গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্টস’-এ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য আইএমএফকেই মূল খলনায়ক হিসেবে তুলে ধরেন। এ বইয়ে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের শর্ত হিসেবে আইএমএফের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার কর্মসূচি, উচ্চ সুদহার, বাণিজ্য উদারীকরণ, ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের প্রসার এবং পুঁজি ও মুদ্রাবানিজ্য উদারীকরণ ওই সব দেশে সুফল থেকে কুফলই বেশি বয়ে এনেছে। পাশাপাশি আইএমএফের এসব নীতির সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে স্থানীয় জনগণ। নিজের বই ‘দি হোয়াইট ম্যানস বারডেন: হোয়াই দ্য ওয়েস্ট এফোর্টস টু এইড দ্য রেস্ট হ্যাভ ডান সো মাচ ইল অ্যান্ড সো লিটল গুড’-এ মার্কিন অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ইসটারলি বিশ্বের দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আইএমএফের নেওয়া কর্মসূচির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকাসহ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্য আইএমএফের এসব ঋণদানের শর্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অদূরদর্শী ও অবাস্তব। তিনি আরও বলেন, এসব দেশে ঋণদানের শর্ত হিসেবে আইএমএফের দেয়া পরামর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই দেশের বাস্তব অবস্থা ও মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি যাচাই না করেই প্রণয়ন করা হয়। শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশেই নয়, আইএমএফের দেওয়া শর্তের ভুক্তভোগী হয়েছে গ্রীসের মতো ইউরোপের উন্নত অর্থনীতির দেশও। ২০১৬ সালে অর্থনৈতিক সংকটের সময় আইএমএফের দ্বারস্থ হয় গ্রীস। এ সময় শর্ত হিসেবে কর বৃদ্ধি, পেনশন ও অন্যান্য খরচ কমানোসহ শিল্পের বেসরকারিকরণের শর্ত চাপিয়ে দেয় আইএমএফ। তবে এসব শর্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে গ্রিসের জনগণ। সরকার কৃচ্ছ্র কর্মসূচির ব্যাপারে গণভোটের আয়োজন করে। জনগণ ব্যাপকভাবে না ভোটের মাধ্যমে আইএমএফের শর্ত প্রত্যাখান করে। তারপরও গ্রীসের তৎকালীন সরকার জনমতকে আমলে না নিয়ে আইএমএফের শর্ত বাস্তবায়ন শুরু করে। এর ফলে গ্রীসের গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে হয়।
আইএমএফের কাছে বাংলাদেশ প্রথম ঋণটি নেওয়া হয় ১৯৭৪ সালে। আইএমএফের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঋণের জন্য ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে সংস্থাটির কাছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশিবার গেছে। এই ১০ বছরে বাংলাদেশ পাঁচবার ঋণ নিয়েছে। এরপর ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত কোনো ঋণ নেয়া হয়নি। এরপর ঋণ নেয় ২০০৩ সালে। এরপর ২০১২ সালে ঋণ নিয়েছিল বাংলাদেশ। যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১০০ কোটি ডলার। আইএমএফের ঋণ সবসময়ই শর্তযুক্ত থাকে। এবার সরকারের সঙ্গে যেহেতু আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়নি, তাই শর্তগুলো এখনো সরকারের কাছে অস্পষ্ট। অতীতেও ঋণ দেয়ার সময় ভর্তুকি তুলে নেয়া এবং নানা ধরনের সংস্কারের শর্ত বাংলাদেশকে মানতে হয়েছিল। আইএমএফের ঋণ পেতে এবারও বাংলাদেশকে নানা শর্ত দিয়েছে। যেমন-ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানো, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে বাজেট থেকে আলাদা করা, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং কৃষি ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমানো ইত্যাদি। ঋণের শর্ত হিসেবে আইএমএফের আরোপ করা এসব সংস্কার কর্মসূচিকে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম বা স্যাপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। ঋণ পেতে আইএমএফের প্রেশক্রিপশন অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতা দেশকে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি মানতে হয়। যাকে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম হিসেবে অভিহিত করা হয়। এজন্য আইএমএফ যে শর্তগুলো চাপিয়ে দেয়, তার মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ, জনস্বার্থে ও উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি ব্যয় সংকোচন, নিত্যপণ্য, খাদ্য, জ্বালানি ও কৃষি থেকে ভর্তুকি তুলে দেয়া ইত্যাদি। ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে আইএমএফের এসব শর্ত মানতে দরিদ্র দেশগুলোকে এক রকম বাধ্য করে, যা অনেকটা ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শামিল। অর্থনৈতিক দুর্দশায় দিশেহারা দেশগুলোর পক্ষে এ শর্তের বাইরে যাওয়ার উপায় থাকে না।
আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমের ব্যাপারে ‘কমিটি ফর দি অ্যাবলিশন অব ইলিজিটিমেট ডেবিট’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কোনো রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তাদের ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ব্যবহার করে। শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনায় নয় বরং ভূরাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখেও কোন দেশ ঋণ পাবে আর কোন দেশ পাবে না, তা নির্ধারণ করে থাকে আইএমএফ। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের নামে আরোপ করা ঋণদানের শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহণকারী দেশগুলোর সরকার ও জনগণের জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই আইএমএফের চাপিয়ে দেয়া এসব ঋণের শর্ত আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অ লের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের জন্য দুর্ভোগ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বয়ে এনেছে। কীভাবে আইএমএফের এসব ঋণদানের দেয়া শর্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশগুলোতে দুর্ভোগ নেমে এসেছে, তার একটা উদাহরণ হতে পারে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মিসর। সে সময় মিসরের মার্কিন সমর্থিত আনোয়ার সাদাতের সরকার আইএমএফের দ্বারস্থ হয়। এ সময় ঋণের বিনিময়ে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয়পণ্যের ওপর সরকারি ভর্তুকিত্যাহারের শর্ত প্রআরোপ করে আইএমএফ।
মিসর সরকার তাদের শর্ত মেনে নিলে দেশটিতে রাতারাতি খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। ক্ষুব্ধ জনগণ রাস্তায় নেমে এলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়। মৃত্যু হয় শত শত বিক্ষোভকারীর। তবে শেষ পর্যন্ত জনগণের দাবি মেনে ভর্তুকি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে মিসর সরকারকে সরে আসতে হয়। ঋণ পেতে আইএমএফের দেয়া কঠিন শর্ত পালন করতে গিয়ে মরক্কোতেও সরকারকে জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। ১৯৮১ সালে বন্দরনগরী কাসাবপ্লাংকায় রাস্তায় নেমে আসা জনগণের ওপর সামরিক বাহিনী গুলি চালালে ৬৩৭ জন বিক্ষোভকারী মারা যায়। ৮০-র দশকের শেষে নাইজেরিয়ায়ও একই রকম পরিস্থিতি হয়। সেখানকার দুর্নীতিবাজ সামরিক একনায়ক বাবানগিদা আইএমএফের দ্বারস্থ হন। বিনিময়ে আইএমএফের কঠিন শর্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেন মূল্যবৃদ্ধির দুর্ভোগ। জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যাংকসহ সরকারি অফিস জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। এদিকে ৯০-এর দশকে আইএমএফের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয় ইন্দোনেশিয়ার প্রবল প্রতাপশালী একনায়ক সুহার্তোকেও। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।
আইএমএফের সবচেয়ে বেশি শেয়ারের মালিক হওয়ায় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ভোটাধিকার রয়েছে। ওয়াশিংটনের আইএমএফের সিদ্ধান্তে ভেটো প্রদানেরও ক্ষমতা রয়েছে। ভেটো ক্ষমতা থাকায় আইএমএফের সব সিদ্ধান্তের ওপর যুক্তরাষ্ট্র এক”ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। ২০০০ সালে জি সেভেনটি সেভেন দেশগুলোর সম্মেলনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছিলেন, আইএমএফের কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী যুক্তরাষ্ট্র। আইএমএফ তৈরির উদ্দেশ্য দুর্বল দেশগুলোর উন্নতিকে রুদ্ধ করা। স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট-এর নামে তাদের সংস্কার কর্মসূচি দুই দশক ধরে বিশ্বের দেশে দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা বয়ে এনেছে। আইএমএফ-এর স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট-এর নামে আরোপিত এসব সংস্কার ও কৃ”ছ্রসাধন নীতির মূল বোঝাটা গিয়ে পড়ে মূলত সমাজের গরিব, শ্রমজীবীও কর্মজীবী মানুষের ঘাড়ে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তাদের জীবনযাত্রার খরচই শুধু বাড়ে না, একই সঙ্গে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে তাদের কম মজুরি এবং নিকৃষ্টতর কর্মপরিবেশ মেনে নিতে হয়। আইএমএফের সংস্কার কর্মসূচির কারণে বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বৃদ্ধি পায় শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ এবং মানব পাচারের মতো ঘটনা।
এছাড়া বেড়ে যাওয়া দারিদ্র্যের কারণে সমাজের বিশাল অংশের মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে সম্প্রতি আইএমএফ’র ঋণ পেতে গিয়ে সরকার ডলার, ঋণের সুদহার, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের দাম বাড়িয়েছে। এগুলোর প্রভাবে লাগামহীনভাবে বেড়েছে গণপরিবহণসহ বিভিন্ন পণ্য ও সেবার দাম। বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি কমানো হয়েছে। ফলে ওই সব খাতেও পণ্য ও সেবার দাম বেড়েছে। মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংকুচিত হয়েছে। ফলে বাড়েনি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতির হার কমানো সম্ভবই হয়নি, উলটো এর পালে আরও হাওয়া লেগেছে। মানুষের খরচ বেড়েছে, কিন্তু বাড়েনি আয়। ফলে জীবনযাত্রার মান কমেছে। এসব মিলে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে আইএমএফের শর্তের জ্বালায় জ্বলছে ভোক্তা। তেল গ্যাস বিদ্যুৎ রাজস্ব খাত সহ নানা শর্ত জুড়ে দিয়েছে। আর সরকারও সেগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভোক্তার ওপর চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যা নিয়ন্ত্রণহীন। লেখক : সাংবাদিক